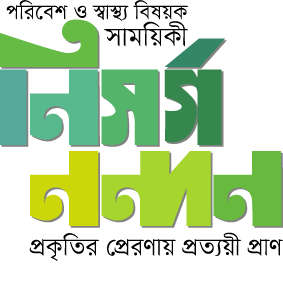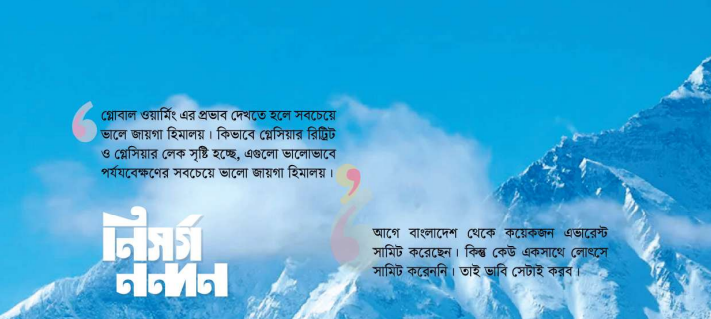মো. দানেশ মিয়া
মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এখন আর দুঃস্বপ্ন কিংবা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। এটি এখন ভয়াবহ বাস্তবতা। মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলেই যে এই পরিবর্তন হচ্ছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। সেই শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন কার্যাবলীর মাধ্যমেই জলবায়ুর এই পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পেছনে কাজ করেছে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্র, মহাসমুদ্রের অম্লতা বৃদ্ধি ও তাদের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন, মেরু অঞ্চলের বড় বড় বরফের চাঁইয়ের অবস্থান ও আকারের পরিবর্তন এবং অতিমাত্রার জলবায়ুগত বিভিন্ন ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি, ইত্যাদি। জলবায়ুতন্ত্রের এই পরিবর্তনের ঝুঁকি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে, যা আরÑফিরেÑআসবেÑনা এরকম একটি স্থানান্তরের দিকে জলবায়ুকে ঠেলে দিবে। গবেষণায় দেখা গেছে, ২১০০
সনের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৫০ সে.মি. থেকে ১০০ সে.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এই হিসাবটি করা হয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিভিন্ন ধরনকে অনুমান করে। সাম্প্রতিক উপগ্রহ ও ভূমিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়েছে যে, ১৯৯৩ সন থেকে আজ পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর প্রায় ৩ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি। জানা গেছে, ১৮৮০ সাল থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ২০ সে.মি. ইতিমধ্যেই বেড়ে গেছে। এই উচ্চতা বৃদ্ধির নিম্নমাত্রার হিসাবটিও যদি সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ (৬০০ মিলিয়ন), যারা নিম্নগামী উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করছে, তারা জল নিমজ্জনের মধ্যে পড়বে।
বাংলাদেশ সম্পর্কেও অনেক ভয়াবহ চিত্র ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় তাপমাত্রা ও ভারী বৃষ্টিপাত, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন ও অন্যান্য ঝড় পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। এতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটা সুষ্পষ্ট ঋণাত্মক পরিবর্তন শুরু হয়েছে বলে আমরা প্রায় সবাই একমত। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপরিভাগের তাপমাত্রা যদি ক্রমবর্ধমান থাকে তাহলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, ২০৫০ সনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের গড় উচ্চতা প্রায় ৩০ সে.মি. বাড়বে এবং এতে প্রায় ১৪ শতাংশ স্থলভূমি স্থায়ী ও অস্থায়ী জল-নিমজ্জনের শিকার হবে।
সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়, মাঝারি গোছের জলবায়ু পরিবর্তনেও বিশেষ করে গরিব দেশ ও গরিব সমাজের মানুষ বেশী মাত্রায় অরক্ষিত হয়ে যেতে পারে। তাপমাত্রা যদি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে গরিব দেশগুলোর পক্ষে এই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে পড়ছে। বর্তমান বংশধরদের উপর যেমনটা পড়ছে, তা ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর পড়বে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। মানব সমাজের ওপর যেরকমভাবে পড়ছে, প্রকৃতির অন্যান্য অংশের ওপর তা ভিন্ন আঙ্গিকে পড়ছে।
বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দ্রুত, অব্যাহত ও কার্যকরী বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ভয়াবহ এই জলবায়ু পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর
লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য বর্তমান সময়টাতেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে, তা না হলে ২০৫০ সনের লক্ষ্যে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। এই কর্মকাণ্ড যদি ধীর গতিসম্পন্ন হয়, তাহলে তা মানিয়ে চলা ও পরিবর্তন ঠেকানোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচকে সুষ্পষ্টভাবে অনেকগুণে বাড়িয়ে দিবে।
এই পরিবর্তনটি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, হঠাৎ করে একে ঠেকিয়ে দেয়া অসম্ভব। তবে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের মাত্রাকে হয়তো প্রশমন করা যেতে পারে। তাই পৃথিবীর অসংখ্য বিজ্ঞানী ও নীতি নির্ধারকগণ কঠিনভাবে ভেবে দেখছেন, কিভাবে জলবায়ুর এই পরিবর্তনকে প্রশমন করা যায়। প্রশমনের জন্য বেশ কয়েকটি কর্মপ্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কাজও চলছে। কিন্তু প্রশমনের দায়-দায়িত্ব হচ্ছে তাদের, যারা ব্যাপক শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন করে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেছে এবং করছে। উল্লেখ্য, এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নই (এষড়নধষ ধিৎসরহম) হচ্ছে বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। এটি আশার কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া প্রায় সবগুলো উন্নত দেশই তাদের দায়-দায়িত্বগুলো স্বীকার করে নিয়ে প্রশমনের কাজ করছে। যেহেতু প্রশমন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন, তাই ইতিমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে পড়ছে।
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। প্রশমনের কোন নৈতিক দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশের না থাকলেও মানিয়ে চলার দক্ষতা অর্জন করা আমাদের টিকে থাকার জন্য জরুরি। আজকে এমন একটি জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক নয়া সমাজ ব্যবস্থার দিকে আমরা এগুচ্ছি, যেখানে সুন্দর, দুর্নীতিমুক্ত ক্রমঃঅগ্রসরমান অর্থনীতির
সাথে সুস্থ একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ধনাত্মক সম্পর্ক আছে, তা মোটামুটি আমরা সবাই বুঝতে পারি। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যস্ততার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সম্পর্ক কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়ছে, তা রাজনৈতিক অর্থনীতিতেও (চড়ষরঃরপধষ ঊপড়হড়সু) প্রভাব ফেলছে পৃথিবীর অনেক দেশে। পৃথিবীতে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত নানান মহামারী এবং বৈশ্বিক মহামারী কোন না কোনভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষয় হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। বর্তমান কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারীর শুরুটা হয়েছে যে ভাইরাসের (ঝঅজঝ-ঈড়ঠ-২) কারণে, তার সাথেও পরিবেশ বিপর্যস্ততার একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আমরা মনে করছি।
প্রশমনের জন্য বেশ কয়েকটি কর্মপ্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কাজও চলছে। ১৯৯৭ সনে কিউটো প্রটোকল অনুসারে গৃহীত সিডিএম (ঈউগ- ঈষবধহ উবাবষড়ঢ়সবহঃ গবপযধহরংস) ও জেআই (ঔও- ঔড়রহঃ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ) হচ্ছে এরই দুটি ‘নমনীয়’ কর্মপদ্ধতি। এই কর্মপদ্ধতি অনুসারে ইতিমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমনের কাজ চলছে পৃথিবীব্যাপী। সম্প্রতি রেড+ (জঊউউ+: জবফঁপরহম বসরংংরড়হং ভৎড়স ফবভড়ৎবংঃধঃরড়হ ধহফ ভড়ৎবংঃ ফবমৎধফধঃরড়হ ধহফ ঃযব ৎড়ষব ড়ভ পড়হংবৎাধঃরড়হ, ংঁংঃধরহধনষব সধহধমবসবহঃ ড়ভ ভড়ৎবংঃং ধহফ বহযধহপবসবহঃ ড়ভ ভড়ৎবংঃ পধৎনড়হ ংঃড়পশং রহ ফবাবষড়ঢ়রহম পড়ঁহঃৎরবং) নামের একটি বনভিত্তিক কর্মসূচি চালু করা নিয়ে ব্যাপক কাজ হচ্ছে, যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন নিবৃত্তিসহ বনের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত অনেক উপযোগিতা অর্জন করা সম্ভব হবে।
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। প্রশমনের কোন নৈতিক দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশের না থাকলেও মানিয়ে চলার দক্ষতা অর্জন করা আমাদের টিকে থাকার জন্য জরুরি। সর্বশেষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগে কখনোই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার বিষয়টি কোন সরকার কার্যকরীভাবে চিন্তা করেনি। কিংবা এরকম কোন রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞাও তৈরি হয়নি। বাজেট ২০০৮-২০০৯ এ প্রথমবারের মতো জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ করে ‘মানিয়ে চলার দক্ষতা’ অর্জন করার জন্য কিছু ব্যয় বরাদ্দ করেছিল সরকার এবং আনুষঙ্গিক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা প্রশমন (গরঃরমধঃরড়হ) এবং মানিয়ে চলা (অফধঢ়ঃধঃরড়হ) দুটোতেই কাজে লাগতে পারে।
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার কৌশল নির্ধারণ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এ বাজেটে ‘জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল’ নামে একটি ফান্ড গঠন করার কথা বলা হয়েছিল এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের জন্য ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই বরাদ্দটি পুরো বরাদ্দের মধ্যে একটি নগণ্য অংশ হলেও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ধারণার সাথে সরকার যে সর্বপ্রথম একটি কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা বলা যায় এবং তা যে পরবর্তী সরকারকে সামনে এগুনোর পথ দেখিয়েছে, তাও হলফ করে বলা যায়।
বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপকভাবে ভাবছে, বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা করছে; পরিবেশ অধিদপ্তরের ‘জলবায়ু পরিবর্তন কোষে’ মানিয়ে চলা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে; ‘পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমূলক’ নতুন কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। আমরা এজন্য একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের সবার প্রত্যাশা থাকবে বর্তমান ও আসন্ন বাজেটে যেন আগের থেকে আরো বেশী বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় এবং জাতীয় সংসদে
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কার্যকরী আলোচনা করা হয়।
পৃথিবীব্যাপী বনের ধ্বংসযজ্ঞ ২০-২৫ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী। এই ধ্বংসযজ্ঞের বেশীরভাগই হচ্ছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও ক্রান্তীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। বাংলাদেশের বনধ্বংসও এক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখেনি।
দেশের মোট ভূ-ভাগের ১৭ শতাংশ বনভূমি কাগজে-কলমে থাকলেও বেশকিছু বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে বন আইনের সঠিক ব্যবহার ও পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাবে। এখানে দুর্নীতিও উল্লেখযোগ্য। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের শালবন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবার পথে। গত তিন-চার দশকে বিভিন্ন প্রভাবশালী বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলের ছত্রছায়ায় বনজ সম্পদকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় ১০ শতাংশ বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বন বলতে সত্যিকার অর্থে যা বুঝায়, তা ২-৩ শতাংশের বেশি হবে না। একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য একটি দেশের মোট ভূ-ভাগের ২৫ শতাংশ সত্যিকার অর্থে বনভূমি থাকা যেমন জরুরি, আজকের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এর প্রশমনের জন্যও অত্যধিক জরুরি শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে। বর্তমান সরকারের কাছে সকল জনগণের প্রত্যাশা এটাই থাকবে যেন সারাদেশের গ্রাসকৃত বনভূমিগুলো উদ্ধার করে নতুন বনাচ্ছাদন সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং বনগ্রাসকারীদেরকে কোনরকম আনুকূল্য না দেখিয়ে তাদের উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কেউ যেন বন ধ্বংসের উৎসবে মেতে না উঠে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে সর্বাগ্রে।
জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, খাদ্যসংকটের বিশাল ভীতির প্রেক্ষাপটে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস না করার যে নীতি, তাতে মোট ভূমির ২০ শতাংশে বনায়নের যে লক্ষ্য বাংলাদেশ সরকারের আছে, তা হয়তো বাস্তবসম্মত নয়। ন্যূনপক্ষে বেদখল হয়ে যাওয়া সরকারি বনভূমিগুলো যদি আমরা ফিরে পাই এবং বনভূমিগুলোকে শুধুমাত্র বনজসম্পদ উৎপাদনেই ব্যবহার করতে পারি, তাহলেও আমরা শেষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসতে পারবো। এজন্য বনবিভাগের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকেই শুধু নয়, প্রভাবশালী মহল যারা রাজনীতির ছত্রছায়ায় কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ হতে বাধ্য করেছে, তাদেরকেও কঠিন বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।
যারা দুর্নীতির প্রচণ্ড একটি আবহের মধ্যে থেকেও দূর্নীতি করেনি, তাদেরকেও খুঁজে বের করে পুরস্কৃত করতে হবে। তাহলেই ন্যায়, নৈতিকতা ও মেধার বিকাশ ঘটবে। এই প্রত্যাশাটি আমরা বর্তমান সরকারের কাছে করতেই পারি।
সমগ্র মানব সমাজের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াটি বেশ খানিকটা জটিল। এই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার বিষয়টিও তাই বেশ খানিকটা কঠিন ও জটিল। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবর্তনের যে আঞ্চলিক মডেল আছে, সে মডেল অনুসারে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সেক্টরে কোন সময় কতটুকুন প্রভাব পড়বে, তা হিসাব করে মানিয়ে চলার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য ব্যাপক গবেষণা করতে হবে। আমাদের দক্ষতা ও অর্থের অভাবে বাংলাদেশে এরকম গবেষণা খুবই কম হচ্ছে বলে আমার ধারণা। প্রয়োজনে বিদেশি সাহায্য নিয়ে গবেষণার ব্যাপকতা ও গভীরতা বাড়াতে হবে।
জলবায়ু পরিবর্তনের দায় আমাদের নয়, এই দায় শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছি আমরা। সেজন্য মানিয়ে চলার জন্য আমাদের যত গবেষণা এবং পরিবর্তিত জীবন আচরণের জন্য যা যা দরকার, তার সবটুকুই দায়ি-দেশগুলোকে আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে।
আমাদের প্রত্যাশিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ধারণাটি আজকে ষ্পষ্ট হতেই হবে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার সাথে যদি আমরা কার্যকরীভাবে মানিয়ে না চলতে পারি, তাহলে কোন অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনাই সত্যিকারভাবে সফল হবে না। বছর বছর বন্যা, সাইক্লোন ও অন্যান্য পরিবেশ- বিপর্যয় যে দারিদ্র্য বাড়ায়, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা যে ব্যাহত হয়, তা আজকে স্পষ্ট। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নিমজ্জমান স্থলভূমি ও ক্রমবর্ধমান লবনাক্ততা যে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ও সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যাপক পরিবর্তন করে দেবে, তা যদি ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে আমরা এখনি বুঝতে চেষ্টা না করি, তাহলে আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। এবং এতে যেকোন সরকারকেই ব্যর্থতার দায় নিতে হবে।
বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের বিনীত প্রত্যাশা থাকবে, একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, তা বিবেচনায় রেখে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পথটি যেন বাছাই করে নেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি আমরা চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে আমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে, ক্রমান্বয়ে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি পতিত হবো। এর হয়তো কোন কার্যকরী সমাধান থাকবে না তখন। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সবরকম পদক্ষেপ নেয়ার আমাদের এখনই সময়।
লেখক : অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সাইয়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়